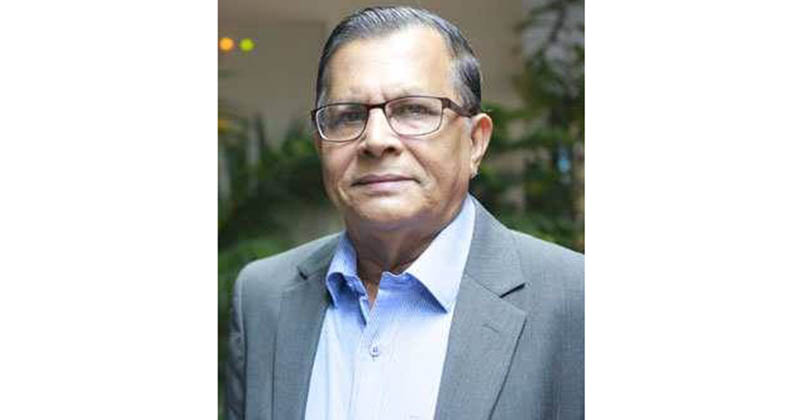সম্প্রতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে সংগতি রেখেই মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং এই মুহূর্তে প্রধান লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় বললেন, ‘জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ কম হলেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।
যেকোনো উপায়ে দেশে ডলার প্রবাহ বাড়াতে হবে। এ মুহূর্তে এর কোনো বিকল্প নেই।’ স্মর্তব্য, অতিমাত্রায় প্রবৃদ্ধিতাড়িত না হয়ে চাহিদা সংকোচন নীতিমালার আওতায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দিয়ে আসছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা। যা হোক, ‘বেটার লেট দ্যান নেভার’, সেই সূত্রে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক আবারও নীতি সুদহার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে তা ৮ শতাংশে উন্নীত করেছে, যা স্মরণ করা দরকার, চলতি অর্থবছরের শুরুতে ছিল ৬ শতাংশের ঘরে।
মুদ্রানীতির এপিঠ-ওপিঠবিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, “নতুন মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির হার ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, নতুন মুদ্রানীতির ধরন হলো ‘সতর্ক ও সংকুলানমুখী’। এর প্রধান লক্ষ্য টাকাকে আরো দামি করে তোলা। অর্থাৎ সুদহার বাড়িয়ে অর্থের প্রবাহে আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ। এ জন্য বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যও কমানো হয়েছে। আগামী জুন পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে মাত্র ১০ শতাংশ। অর্থবছরের শুরুতে এই লক্ষ্যমাত্রা ১১ শতাংশ রাখার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল।”
সাধারণত সুদহার বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণপ্রবাহ কমে গেলে বেসরকারি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প চলমান পুঁজির অভাবে সংকটে নিপতিত হয়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার আমাদের আশ্বস্ত করে বলছেন, ‘কৃষি, সিএসএমইসহ বিভিন্ন খাতের জন্য আমরা পুনরর্থায়ন তহবিল গঠন করেছি। এ খাতগুলো যাতে ঋণবঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্য নিয়েই তহবিলগুলো গঠন করা হয়েছে। আশা করছি, বেসরকারি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আমদানি ঋণপত্র খুলতে না পারার কারণে কিছু ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটির নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আমাদের হাতে কোনো বিকল্প ছিল না। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলারের এলসি খোলা হয়েছিল। এত বিপুল পরিমাণ আমদানির প্রয়োজন ছিল কি না, সেটি নিয়েও প্রশ্ন আছে। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা না হলে পরের অর্থবছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আমদানি এলসি খোলা হতো। এতে দেশের রিজার্ভ এখন যা আছে, তা-ও থাকত না।’
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতির লক্ষ্য অর্জিত হয়নি—না মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, না ব্যক্তি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার বিষয়ে গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, ‘মূল্যস্ফীতির উচ্চহারসহ অর্থনৈতিক সংকটগুলো এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। এগুলোর সমাধান হতেও সময় লাগবে। মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদহার বাড়ানো হয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাজারে এর প্রভাব দৃশ্যমান হবে।’ আমরা আশা করছি যে গভর্নরের প্রত্যাশা পূরণ হয়ে জনজীবনে স্বস্তির সুবাতাস বইবে।
ব্যাংক খাতের সুশাসন ফেরানোর পাশাপাশি খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগের বিষয়ে গভর্নর বলেন, ‘ব্যাংক খাতে সুশাসন বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করছে। এ বিষয়ে বেশ কিছু নীতিমালাও প্রস্তুত করা হচ্ছে। নতুন সরকারের সঙ্গে নীতিমালাগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। শিগগিরই এসব জারি হতে পারে।’
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে রিজার্ভের ওপর চাপ কমার দাবি করা হচ্ছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, এখনো রিজার্ভের ক্ষয় বন্ধ হয়নি। গভর্নর বলেন, ‘বাংলাদেশের চলতি হিসাব সব সময়ই ঘাটতিতে ছিল। চলতি হিসাব থেকে উদ্বৃত্ত ডলারে আমাদের রিজার্ভ বাড়ত না। আমাদের রিজার্ভ বাড়ত ফিন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্টের উদ্বৃত্ত থেকে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফিন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্টে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এই ঘাটতির কারণ বৈদেশিক দান-অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়া। দেশের স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণের বড় অংশ পরিশোধ হয়ে গেছে। এ কারণে বিদেশি ঋণের স্থিতি কমেছে। এ মুহূর্তে ঋণ পরিশোধের খুব বেশি চাপ নেই। আমাদের রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় স্থিতিশীল থাকলে ভবিষ্যতে রিজার্ভ বাড়বে। জাতীয় নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও কেটে গেছে। আশা করছি, বিদেশি বিনিয়োগও বাড়বে।’ তবে মুদ্রানীতি একাই চলমান সব সমস্যার সমাধান দিতে পারবে বলে মনে হয় না। আমরা ব্যাট ও বলের মধ্যকার এই সংযোগহীনতার পেছনের কারণ নিয়ে দু-একটি কথা বলতে পারি।
প্রথমত, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের ব্যাংকের সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই বলে মুদ্রানীতির সফলতা নিয়ে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন করে না এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, ‘বাংলাদেশের অর্থনীতি যে চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কেবল পলিসি রেট বাড়ালে খুব একটা কার্যকর কিছু হবে না। গত দুই বছরে এমন পদক্ষেপের কোনো ফল আমরা দেখিনি। অর্থাৎ মানুষের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে পলিসি রেট এতটা প্রভাব রাখে না। পশ্চিমা বিশ্বে দেখা গেছে, শতভাগ মানুষ ব্যাংকিং সেবার আওতায়। সেখানে সুদহারের প্রভাব পড়ে।’
তিনি আরো মনে করেন, বাংলাদেশে রেপো রেট বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কারণ আমাদের মূল্যস্ফীতি সরবরাহজনিত মূল্যস্ফীতি, চাহিদা চাঙ্গা হওয়ার জন্য নয়। আরেকটি দিক হলো, শুধু মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করলে বড় কিছু হবে না। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে, ফিন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্ট এখন নেতিবাচক। রপ্তানি আয় বাড়ানো ও বৈচিত্র্যকরণের জন্য কিছু পলিসি দরকার ছিল মুদ্রানীতিতে। তৈরি পোশাকের বাইরে অন্যান্য খাতে রপ্তানি উৎসাহিত করতে প্রণোদনা থাকলে ভালো হতো। শুধু মূল্যস্ফীতি কমানো হবে আর অন্য ক্ষেত্রে কিছু করা হবে না, এতে আংশিক সমস্যার সমাধান হবে। বিষয়টি হলো, সার্বিকভাবে সমস্যার গভীরে গিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত ছিল।
মুদ্রানীতি নিয়ে আলোচনায় যা আড়ালে থেকে যায় তা হলো এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক এককভাবে মূল্যস্ফীতি কমাতে পারে না। মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি : ক. বাজার সঠিকভাবে মনিটর করতে হবে; খ. বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; গ. চাঁদাবাজ, অসৎ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য দূর করতে হবে। আর এগুলো করতে গিয়ে কঠোর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে।
মোটকথা, বাংলাদেশ ব্যাংক তো নীতি সুদ হার ঠিক করে দিল। এখন বাণিজ্য, খাদ্য ও কৃষিÑ এই তিন মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে চেষ্টা করতে হবে বাজারকে বাগে আনার জন্য। বিশেষভাবে এই জায়গাটায় সরকারি ব্যর্থতা সবার নজর কাড়ে। কয়েকটা দোকানে গিয়ে অভিযান, জরিমানা করে তেমন একটা পরিবর্তন আসবে বলে বিজ্ঞজনরা মনে করেন না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মতে, আইনের শাসন, তদারকি দিয়ে বাজারে সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না করে শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না। এই মুহূর্তে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতির পাশাপাশি চাই শিষ্টের লালন এবং দুষ্টের দমন। একটি বিকৃত বাজার ব্যবস্থায় যত ভালো মুদ্রানীতি হোক না কেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কাজটি বড় কঠিন।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, সাবেক উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়