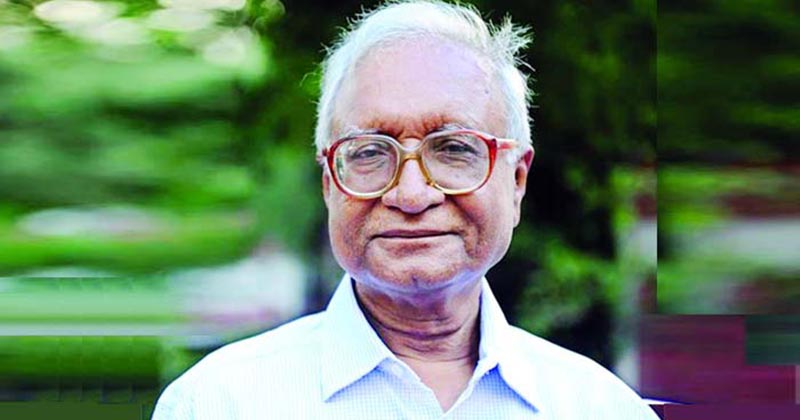ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে আমার ভর্তি হওয়াটা ঘটেছিল ছোটখাটো একটি গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আমার পিতা চেয়েছিলেন আমি পড়ি অর্থনীতিÑ যাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ায় সুবিধা হয়। সেকালে ওটাই হতো প্রথম নির্বাচন, ব্যর্থ হলে অন্যপথ খোঁজা। কিন্তু আমার পক্ষপাত তো সাহিত্যের দিকে। অনড় দুপক্ষে শেষ পর্যন্ত একটি সমঝোতা হয়েছিল এই মর্মে যে, আমি বাংলা নয়; ইংরেজি সাহিত্য পড়ব, সাবসিডিয়ারি হবে পলিটিক্যাল সায়েন্স ও ইকোনমিক্সÑ যাতে সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রস্তুতিটা চলতে থাকে। সাহিত্যের ব্যাপারে আমার আগ্রহটা ছিলÑ পরে বুঝেছি, ওই যুক্ত হওয়ার তাড়নাতেই। তা ভর্তি হয়েই আমি নানাভাবে যুক্ত হয়ে গেলাম। অল্প পরই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে গিয়েছি দেখতে পেলাম এবং জিতলামও। পরের তিন বছরও হল সংসদ নির্বাচনে তুমুলভাবেই অংশ নিয়েছি।
আবাসিক ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু ঘোরাফেরা ছিল ছাত্রাবাসেই। আর নির্বাচন এলে তো আমাকে যুক্ত হতেই হতো। সেকালে প্রার্থীদের পরিচয়পত্র লেখা হতো ইংরেজিতে। আমার ওপর দায়িত্ব বর্তায় প্রেস থেকে সম্মিলিত পরিচয়পত্র ছাপিয়ে আনার। একবার তো আমার সারারাতই কেটেছে প্রেসে। খুব সকালে ছাপানো বুকলেট প্যাকেটে করে নিয়ে হলে গিয়েছি। এতে অন্যরা কতটা উৎফুল্ল হয়েছে, তা জানা হয়নি। তবে আমি যে গৌরব অনুভব করেছি, এতে সন্দেহ নেই। নির্বাচনের দিন মাইক্রোফোনে প্রবল প্রচার চলত। এতেও আমার সক্রিয় অংশগ্রহণে কোনো ত্রুটি ছিল না।
প্রতিটি আবাসিক হলেরই একটি সাংস্কৃতিক জীবন ছিল। প্রতিবছর প্রতিযোগিতা হতো আবৃত্তি, বক্তৃতা, গান ইত্যাদির। আমি গান বাদ দিয়ে অন্যগুলোয় অংশ নিতাম। হল বার্ষিকী বের হতো। এতে আমি লিখেছি। বার্ষিকী সম্পাদনাতেও একবার যুক্ত হয়েছিলাম। ওই লেখা ও সম্পাদনার কাজটায় ছিল আমার বিশেষ আগ্রহ। ভালো-মন্দ যা-ই হোক, আমি লিখতাম এবং হাতে লেখা পত্রিকা, দেয়াল পত্রিকা, ছাপা পত্রিকাÑ অনেক কিছুই সম্পাদনার দায়িত্ব নিজ থেকেই নিয়ে নিয়েছি। আসলে এর ভেতরেও ছিল অন্যদের সঙ্গে সংলগ্ন থাকার আগ্রহ। আমি লিখছি, অন্যরা দেখছে, হয়তো পড়ছেওÑ এটি একটি ভরসার ব্যাপার ছিল। কেননা ভেতরে ভয় ছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার।
একাকী থাকতে যে আমার ভীষণ রকম অপছন্দ ছিল, তা নয়; কখনো কখনো ভালোই লাগত। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব- এটি ছিল রীতিমতো একটি আতঙ্ক, দুঃস্বপ্নের মতো; যেন হারিয়ে যাব। আর ওই যে পত্রিকা সম্পাদনার কর্ম, এতে দেখতাম আমি অনেকের সঙ্গে আছি। একসঙ্গে কাজ করছি, পত্রিকা বের করে তা বিতরণ করছি, দলবেঁধে বের হয়েছি বিজ্ঞাপন জোগাড়ে, প্রুফ দেখছি প্রেসে বসেÑ সবটাতেই সংযোগ ঘটছে অন্যদের সঙ্গে। ঠাট্টা করে আমার বন্ধু আবদুল বারি তো আমাকে ‘দি এডিটর’ বলেই ডাকত।
হাতে লেখা পত্রিকাতেও আনন্দ ছিল। ‘রাঙা প্রভাত’ নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের করতেন ঢাকা কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র মিলে। এর সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আবদুল কাদির। তিনি আমাদের দুই বছরের সিনিয়র ও প্রতিবেশী। তিনিই আমাকে দায়িত্ব দিলেন দ্বিতীয় সংখ্যাটি বের করার জন্য। অনেকগুলো রচনা তিনিই এনে দিয়েছিলেনÑ যার মধ্যে ছিল মুনীর চৌধুরীর গল্প ও শামসুর রাহমানের কবিতা। সহায়তা করেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। পাড়ায় তখন আর্ট কলেজের কয়েক ছাত্র থাকতেন। তাদের মধ্যে দুজন জুনাবুল ইসলাম ও হুমায়ুন কাদির অলঙ্করণ করে এবং প্রচ্ছদ ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।
এদিকে সবেগে চলছিল ছাত্রসংঘের কাজ। আমরা ছেলেরা ছাত্রসংঘ গড়েছি পাড়ায়, পাঠাগার খুলেছি, ছেপে পত্রিকা বের করেছি কষ্টে-সৃষ্টে। পাঠাগারে সাহিত্যসভা বসত প্রতিসপ্তাহে। মঞ্চ তৈরি করে এতে নাটক, বিচিত্রা অনুষ্ঠান, ছায়ানাটকÑ এসব করেছি, লিখছিও। আমি দেখতে পাই যে, লেখা নিয়ে যাচ্ছি তখনকার প্রধান মাসিক পত্রিকা ‘মাহে নও’ অফিসে। লিখে কিছু আয়ও হচ্ছে। অংশ নিচ্ছি রেডিও প্রোগ্রামে। রেডিওর এক প্রযোজকের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ইবসেনের ‘ওয়াইল্ড ডাক’-এর একটি রূপান্তরও দাঁড় করে ফেলেছি। সেটি প্রচারও হয়েছে। রেডিওতে অনুষ্ঠান করলে নগদানগদি একটি চেক পাওয়া যেত। তবে সেটি ভাঙানোর জন্য ছুটতে হতো সদরঘাটে। সেখানে তখন রয়েছে স্টেট ব্যাংক।
আমার প্রধান বিনোদন ছিল পড়া। যা পাই, তা-ই পড়ি। পড়া আমাকে হাতে ধরে নিয়ে পার করে দিয়েছে বিচ্ছিন্নতার সীমান্ত থেকে। আমার জন্য মস্তবড় আকর্ষণের জায়গা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গ্রন্থাগারটি। সেলফের কাছে যেতে পারি না, সিøপ দিয়ে বই আনতে হয়। গ্রন্থাগারের ভেতরের জগৎটিকে মনে হয় রহস্যময়। দ্বিতীয় বর্ষেই যখন আমার চশমা নেওয়ার দরকার পড়ল, তখন আমার বাবা বললেনÑ পেঙ্গুইনের ছোট ছোট অক্ষরের বই পড়তে গিয়ে ছেলেটার এ দশা। নিতান্ত ভুল বলেননি। পেঙ্গুইনে তখন গুরুত্বপূর্ণ সব বই-ই পাওয়া যেত আর দামও ছিল খুব কম। বৃত্তির টাকা পেলেই প্রথমে ছুটতাম বইয়ের দোকানে। এখন যেখানে শহীদ মিনার, এর উল্টোদিকে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বইয়ের দোকান ছিল। মালিকরা জানতেন কোন বই চলবে, কোনটি চলবে না; ওই অনুযায়ী পেঙ্গুইনের বই বেশ আনতেন। কিন্তু প্রচুর নয়। মনে পড়ে, টিএস এলিয়টের ‘সিলেকটেড এসেজ’ এসেছে শুনে প্রায় দৌড়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি দুই কপি মাত্র আছে। আমি দ্রুত এক কপি হস্তগত করে ফেলেই আবিষ্কার করি শামসুর রাহমানও এসে গেছেন। তিনি আমাদের তিন ক্লাস উপরে পড়তেন ইংরেজি বিভাগেই। তারও লক্ষ্যবস্তু এলিয়টের ওই বই। দ্বিতীয় কপিটি তিনি নিয়েছিলেন। আমাদের তখনকার এ ঢাকা নামক মফস্বল শহরে বই পাওয়াটা মোটেই সহজ ছিল না।
আমাদের ওইকালে আমরা যে কেবল শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও বইপুস্তকপ্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধার দিক থেকেই সীমিত ছিলাম, তা নয়; আমাদের পাঠ্যসূচিও ছিল বেশ দরিদ্র, কিছুটা মফস্বলীয়। অনার্সে আমরা পুরো একটি পেপার অ্যাংলো-স্যাকসন লিটারেচার পড়েছি। সেখানে প্রাচীন ভাষাও পড়তে হয়েছেÑ যা খুব কাজে লেগেছে বলে মনে হয় না। আবার এমএতে ছিল একশ নম্বর মিডল ইংলিশ। এ দুইকে এক করে খালি জায়গায় যদি শেকসপিয়র পড়ানো হতো একটি স্বতন্ত্র পেপার হিসেবে, তা হলে আমরা অধিক উপকৃত হতাম। আমরা এইটিন্থ সেঞ্চুরি লিটারেচার পড়েছি। তবে ‘টম জোনস’ পড়িনি। সবচেয়ে দুর্বল ছিল মর্ডান পেপার। সেখানে ঔপন্যাসিক হিসেবে অলডাস হাক্সলি ও সমারসেট মম ছিলেন; ছিলেন না জোসেফ কনরাড, ইএম ফরস্টার কিংবা ডিএইচ লরেন্সÑ তিনজনের একজনও নয়।
শেষ করি এ কথাটি বলে যে, গত একশ বছরে ইংরেজি বিভাগ থেকে অনেক যশস্বী ব্যক্তি বের হয়েছেন। তাদের স্মরণ করা হয়, স্মরণ করাটা দরকারও। কিন্তু আমরা যেন না ভুলি লীলা নাগকেÑ যিনি কেবল ইংরেজি বিভাগেরই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রথম ছাত্রী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সময়ের প্রথম ও একমাত্র নারী পোস্টগ্র্যাজুয়েট তিনি। ভর্তি হয়েছিলেন অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রীশূন্য অবস্থায় যাত্রা শুরুর লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে। পরে তিনি জনমুক্তির সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে যুক্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতি করেছেন, রাজবন্দি ছিলেন দীর্ঘকাল; নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য ঢাকা শহরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সম্পাদনা করতেন মাসিক পত্রিকা। বিভাগে তার সহপাঠী অনিল রায়ও ছিলেন রাজনীতিমনস্ক। দুজনেই সুভাষ বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী ছিলেন তারা ব্যক্তিগত জীবনে।
স্মরণ করা দরকার আরও দুজন শিক্ষককে। অমলেন্দু বসু ও অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় বিভাগীয় শিক্ষক অমলেন্দু বসু ডক্টরেট করছিলেন অক্সফোর্ডে। তিনি আর ঢাকায় ফেরেননি। অমলেন্দু বসু ছিলেন পূর্ববঙ্গেরই মানুষ। অভিয়ভূষণ চক্রবর্তী দেশভাগের পরও কিছুদিন ছিলেন। তিনিও পূর্ববঙ্গীয়। স্থায়ীভাবে থাকবেনÑ এমন ভাবনা নিশ্চয়ই তার ছিল। কিন্তু পারলেন না। কারণ তার যোগ ছিল গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে; ঢাকায় থাকলে হয়তো সাহিত্যের বস্তুবাদী ধারার ব্যাখ্যা চালু রাখতে পারতেনÑ আর্নল্ড কেটল যেমনটা রেখেছিলেন লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে।
লেখক : শিক্ষাবিদ ও ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়